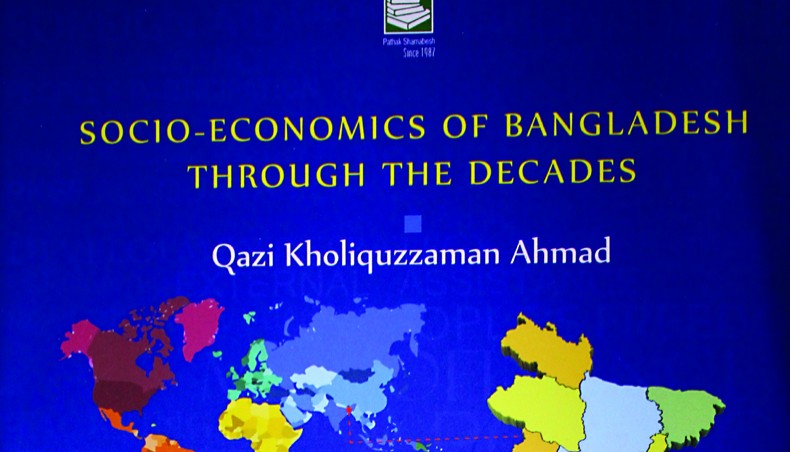দৈনিক সমকাল: প্রিন্ট সংস্করণ, প্রকাশ : ১৪ মে ২০১৫
কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ
চার দশকের বেশি সময় ধরে ঝুলে থাকা ভারত-বাংলাদেশ স্থল সীমান্ত চুক্তি বিল প্রথমে ভারতের মন্ত্রিসভায় অনুমোদন এবং পরে রাজ্যসভা ও লোকসভায় ৭ই মে ২০১৫ তারিখে ‘সর্বসম্মতিক্রমে’ অনুসমর্থন দুই দেশের জন্য বড় অর্জন। বিলম্বে হলেও চুক্তিটি অনুসমর্থনের জন্য ভারতকে অবশ্যই সাধুবাদ জানাতে হবে; কিন্তু একই সঙ্গে মনে রাখতে হবে, এটা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ট নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ সরকারেরও বিশাল কূটনৈতিক সাফল্য। এটাও লক্ষণীয়, টানা দ্বিতীয় মেয়াদে ক্ষমতায় থাকার কারণেই চুক্তিটি স্বাক্ষরের ব্যাপারে ভারতের ওপর কূটনৈতিক চাপ অব্যাহত রাখা সম্ভব হয়েছে।
শেখ হাসিনার সরকার দ্বিতীয় মেয়াদে ক্ষমতায় না থাকলে, এভাবে সীমান্ত সমস্যার সমাধান হতো কি-না, আমি নিশ্চিত নই। আমরা দেখেছি, ১৯৭৪ সালে ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী এবং বাংলাদেশের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান চুক্তিটি স্বাক্ষর করেছিলেন। কিন্তু পঁচাত্তরের শোকাবহ ১৫ আগস্টের পর পরিস্থিতি সম্পূর্ণ পাল্টে গিয়েছিল। পঁচাত্তর-পরবর্তী সরকারগুলোর না ছিল কূটনৈতিক দূরদর্শিতা, না ছিল চুক্তিটি অনুসমর্থনের ব্যাপারে ভারতকে প্রভাবিত করার ক্ষমতা। বরং পরবর্তী দুই দশক ধরে ক্ষমতাসীন সরকারগুলো এই চুক্তি নিয়ে নানা বিভ্রান্তি ও অপপ্রচার চালিয়েছে। নিয়তির পরিহাসই বলতে হবে যে, বাংলাদেশে যেসব রাজনৈতিক পক্ষ পঁচাত্তর-পরবর্তী সময়ে মুজিব-ইন্দিরা চুক্তিকে ‘গোলামি চুক্তি’ আখ্যা দিয়ে প্রপাগান্ডা চালিয়েছে, তারাই এখন এটাকে স্বাগত জানাচ্ছে!
স্থল সীমান্ত চুক্তি ভারতের রাজ্যসভা ও লোকসভায় অনুমোদন হওয়ার জন্য দেশটির বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে অবশ্যই কৃতিত্ব দিতে হবে। তিনি পশ্চিমবঙ্গ ও আসামে এই চুক্তির বিরোধিতা কার্যকরভাবে নিরসন করতে পারলেন । কিন্তু ভুলে যাওয়া চলবে না পূর্ববর্তী ইউপিএ সরকারের কথা। মনে রাখতে হবে, মনমোহন সিংয়ের নেতৃত্বাধীন সরকারই নানা বিরোধিতা সত্ত্বেও চুক্তিটি রাজ্যসভায় উত্থাপন করেছিল। এ ক্ষেত্রে কংগ্রেস প্রধান সোনিয়া গান্ধী পালন করেছিলেন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা।
চুক্তিটি এই পর্যায়ে আসার জন্য কার কেমন ভূমিকা ছিল, তার মাত্রা নিয়ে বিতর্ক থাকতে পারে; কিন্তু এটা অবিসংবাদিত যে, এর মধ্য দিয়ে স্পষ্ট হয়েছে যে বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক বর্তমানে এক নতুন উচ্চতায় পৌচেছে। বস্তুত এর বিকল্পও নেই। বাংলাদেশ ও ভারতের যে ভৌগোলিক অবস্থান, তাতে করে দুই দেশকেই পরস্পরের প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে হবে। আমাদের অভিন্ন ইতিহাস, সংস্কৃতি শুধু নয়; বিশ্বায়নের এই যুগে প্রতিবেশীদের বাদ দিয়ে কোনো দেশের পক্ষে অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রায় অসম্ভব। অভিন্ন সীমান্ত ছাড়াও দুই দেশের মধ্যে সহযোগিতার আরও অনেক অভিন্ন ক্ষেত্র রয়েছে। কিন্তু সীমান্ত চুক্তিটি ঝুলে থাকায় সেসব ক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত অগ্রগতি সম্ভব হচ্ছিল না। কারণ পারস্পরিক আস্থা, বিশ্বাস ও সহযোগিতার ক্ষেত্রে চার দশক পুরাতন সীমান্ত সংকট বারবারই পেছনে টেনে ধরেছে। এছাড়া দুই দেশের উন্নয়নের ক্ষেত্রে সীমান্তের উভয় পাশের ছিটমহলগুলোর জনসাধারণের জীবনমান ও মানবিক মর্যাদা কাঁটার মতো খচখচ করত। এই চুক্তি ভারতের পক্ষে অনুসমর্থনের পর হাজার হাজার ছিটমহলবাসী সত্যিকার অর্থে রাষ্ট্রীয় পরিচয় পাবে। তারা তাদের মৌলিক চাহিদাগুলো পূরণ করতে পারবে এবং নিজেরাই নিজেদের ভাগ্যোন্নয়নে সক্রিয় হতে পারবে। ছিটমহল বিনিময়ের সিদ্ধান্ত নিশ্চয়ই বিশ্বের বৃহত্তম একটি মানবিক সংকটের অবসানের ক্ষেত্রে মাইলফলক হয়ে থাকে। তবে মনে রাখতে হবে, সীমান্ত চিহ্নিতকরণ বা ছিটমহল বিনিময়কে কেবল মানবিক সংকটের প্রেক্ষিতে দেখলে চলবে না। বস্তুত স্থল সীমান্ত চুক্তিকে সম্ভাবনার সিঁড়ি হিসেবে ব্যবহার করে সহযোগিতার নতুন নতুন দিগন্তের পানে এগিয়ে যেতে হবে। তাহলেই চার দশক ধরে চুক্তিটি অনুসমর্থনের পেছনে বাংলাদেশ ও ভারতের বিভিন্ন মহলের সময়, শ্রম ও প্রচেষ্টা সত্যিকার অর্থে সার্থক হবে। সীমান্ত সংক্রান্ত কারিগরি বিষয়ে এই সদিচ্ছাকে সামনে নিয়ে দুই দেশের আর্থ-সামাজিক সহযোগিতা ও অভিন্ন সম্পদ ব্যবস্থাপনার অভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণের ব্যাপারে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা করতে হবে।
এ ক্ষেত্রে প্রথমেই বলতে হবে দুই দেশের মধ্যে যৌথ সীমান্ত ব্যবস্থাপনার কথা। এখন যেহেতু অচিহ্নিত সীমান্ত থাকবে না, অপদখলীয় ভূমি থাকবে না; সেহেতু বিজিবি ও বিএসএফের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির আশঙ্কা অনেকাংশে কমে যাবে। সীমান্তে যৌথ টহল বা ব্যবস্থাপনা চালু হলে চোরাচালান নিঃসন্দেহে কমে আসবে। আর তাতে করে সীমান্ত এলাকায় দুই দেশের জনগণেরই রক্তপাত নিয়ন্ত্রণে আসবে। সীমান্ত ব্যবস্থা উন্নত হলে মানব পাচারের হারও কমে আসবে। চোরাচালান ও মানব পাচারের সঙ্গে সীমান্ত এলাকার আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ফলে সীমান্তে স্থিতিশীলতার প্রভাব অভ্যন্তরীণ আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতিতেও পড়বে।
দ্বিতীয়ত, দুই দেশের মধ্যে অবকাঠামোগত যোগাযোগ আরও বাড়াতে হবে। এখন সড়ক ও রেলপথে সামান্য যোগাযোগ রয়েছে। এটাকে আরও বাড়াতে হবে এবং বহুমাত্রিক করে তুলতে হবে। ২০১১ সালের সেপ্টেম্বরে ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংয়ের ঢাকা সফরের সময় দুই দেশের মধ্যে স্বাক্ষরিত ফ্রেমওয়ার্ক অ্যাগ্রিমেন্টে বাংলাদেশ ও ভারত ছাড়াও নেপাল ও ভুটানকে নিয়ে চার দেশীয় অবকাঠামোগত যোগাযোগ গড়ে তোলার অঙ্গীকার রয়েছে। এদিকে এখন বিশেষভাবে নজর দিতে হবে। ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় ভূমিবেষ্টিত রাজ্যগুলোর জন্য বাংলাদেশের সমুদ্রবন্দর ব্যবহারের সুযোগ অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে বড় ধরনের উল্লম্ফন ঘটাবে। আবার সমুদ্রবন্দরকে কেন্দ্র করে উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলো ও নেপাল-ভুটানের সঙ্গে অবকাঠামোগত যোগাযোগ বাড়লে বাংলাদেশের জন্যও বড় বাজার সৃষ্টি হবে। এত বড় সুযোগ হেলায় ফেলে রাখা উভয় দেশের জন্যই ক্ষতিকর। সীমান্তের উভয় পাশে যোগাযোগ, যাতায়াত ও বাণিজ্য বাড়লে সীমান্ত এলাকায় দুই দেশের জনগোষ্ঠীর মধ্যে তো বটেই, সামগ্রিক অর্থেই অনাস্থা, অবিশ্বাস কমে আসবে। বাড়বে অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক নৈকট্য। আরেকটি বিষয় হচ্ছে, দুই দেশেরই অভিন্ন শত্রু জঙ্গিবাদ। সীমান্তে অস্থিতিশীলতা থাকলে, সীমান্ত ব্যবস্থা অনুন্নত থাকলে তাদের পক্ষে দুই পাশে যাতায়াত ও জাল বিস্তার সহজ হয়। তারা অস্ত্র ও মাদক চোরাচালানের সঙ্গে জড়িত। সীমান্ত সুরক্ষিত থাকলে জঙ্গিবাদ মোকাবেলাও ঢাকা ও নয়াদিলি্লর জন্য অপেক্ষাকৃত সহজ হবে।
তৃতীয় যে বিষয়টি এখন গুরুত্বপূর্ণ তা হচ্ছে, তিস্তাসহ সব অভিন্ন নদীর পানি বণ্টন বা ব্যবস্থাপনা। স্থল সীমান্ত চুক্তির মতোই তিস্তার পানি বণ্টনের বিষয়টি স্বাধীনতার পর থেকেই ঝুলে আছে। এছাড়া আরও কয়েকটি নদীর পানি বণ্টন নিয়ে দফায় দফায় আলোচনা হয়েছে; কিন্তু উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি নেই। এখন বাংলাদেশ ও ভারত উভয় সরকার তিস্তাসহ অন্যান্য অভিন্ন নদীর ইস্যু মীমাংসার বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দিতে পারে। অভিন্ন নদীর যৌথ ব্যবস্থাপনার সঙ্গে দুই দেশের নৌ যোগাযোগের বিষয়টিও জড়িত। সড়কপথের পাশাপাশি নৌপথে দুই দেশের মধ্যে পরিবহন ও বাণিজ্যের বিপুল সম্ভাবনা অব্যবহৃতই হয়ে গেছে। অভিন্ন নদীর সমস্যাগুলোর নিষ্পত্তির মধ্য দিয়ে দুই দেশ সেদিকে নজর দিতে পারে। এছাড়া অভিন্ন নদীর পানিসম্পদের অভিন্ন ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দুই দেশ পরিবেশ, কৃষি, পর্যটন ক্ষেত্রেও লাভবান হতে পারে। ভারত, নেপাল ও ভুটানের হিমালয় অঞ্চলের নদীগুলোতে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে। ভারত ইতিমধ্যে এই সম্ভাবনা বাস্তবে পরিণত করেছে। বাংলাদেশও অভিন্ন নদীসূত্রে এর সুফল পেতে পারে।
চতুর্থত, বাংলাদেশ ও ভারত যেহেতু একই হিমালয় পর্বতমালার পাদদেশে এবং একই বঙ্গোপসাগরের তীরে অবস্থিত, দুই দেশের দুর্যোগ সংক্রান্ত চিত্রও প্রায় অভিন্ন। বিশেষ করে হিমালয় পর্বতমালা ও বঙ্গোপসাগরকে কেন্দ্র করে জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত ভারত ও বাংলাদেশের জন্য সমান। এই দুর্যোগ মোকাবেলায় দুই দেশকে একযোগে কাজ করতে হবে। সীমান্ত সংকট কেটে যাওয়ার পর এ ধরনের কাজ নিঃসন্দেহে আরও মসৃণভাবে করা যাবে। সেজন্য দুই দেশকে এখন থেকেই পরিবেশ সংকট, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবেলায় যৌথ উদ্যোগ ও কর্মসূচির বিষয়কে অগ্রাধিকারে রাখতে হবে।
পঞ্চম বিষয়টি হচ্ছে, দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য ঘাটতি কমানো ও পারস্পরিক বিনিয়োগ বাড়ানো। ভারতীয় পণ্যের জন্য বাংলাদেশ যথেষ্ট বড় বাজার হলেও ভারতে বাংলাদেশি পণ্যের বাজার সে তুলনায় অনেক কম। ইতিমধ্যে বাংলাদেশি বিপুল সংখ্যক পণ্যের শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কিছু অশুল্ক বাধা এখনও রয়ে গেছে। এগুলোও দ্রুত সরিয়ে ফেলতে হবে ভারতকে। তাহলে বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে দুই দেশই উপকৃত হবে এবং দুই দেশেরই জনসাধারণের জীবনমান উন্নীত হবে। বেসরকারি পর্যায়ে যোগাযোগ ও আদান-প্রদান বাড়ানোও জরুরি। সে ক্ষেত্রে ভারতের ভিসাপ্রাপ্তি সাধারণ মানুষের জন্য বেশ কঠিন। এই প্রক্রিয়া যথাসম্ভব সহজ করে ফেলা উচিত। এমনকি ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী দেশ হিসেবে উভয়পক্ষই ভিসামুক্ত যাতায়াত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতেই পারে।
তবে সবার আগে স্থল সীমান্ত চুক্তির যথাযথ বাস্তবায়নে মনোযোগ দিতে হবে দুই দেশকে। আমি আশা করি, যত দ্রুত সম্ভব চুক্তিটি বাস্তবায়ন ও ছিটমহল বিনিময় সম্ভব হবে। দুই দেশের সরকার কেবল নয়, সব রাজনৈতিক দল, সংবাদমাধ্যম, নাগরিক সমাজ এ ক্ষেত্রে যে সদিচ্ছা ও আন্তরিকতা প্রদর্শন করেছে, তাতে করে আমি আশান্বিত যে, খুব বেশি সময় প্রয়োজন হবে না একটি নেতিবাচক পরিস্থিতি থেকে এভাবে ইতিবাচক উত্তরণের জন্য। আমি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে ধন্যবাদ জানাই। ধন্যবাদ জানাই কংগ্রেস, বিজেপিসহ ভারতের সব রাজনৈতিক দলকে এবং এই প্রক্রিয়ায় যুক্ত সবাইকে।
অর্থনীতিবিদ